মাতৃভূমিঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা - মীজান রহমান
আশ্রম আর লেখক মীজান রহমান (১৯৩২-২০১৫) হরিহরআত্মা, মীজান রহমান ছাড়া আশ্রমের একটি সংখ্যাও প্রকাশিত হয়নি কোনোদিন। আজ মীজান রহমান আমাদের মাঝে নাই। কিন্তু তিনি এমন বহু বিষয় ও লেখা রেখে গেছেন যা পুরনো হয়ে যায়নি আজো। মীজান রহমানের প্রাসঙ্গিক লেখা আমরা ছাপতে চাই এজন্যে যে এমন একজন বিশ্ব-বাঙ্গালি মানবিক চেতনার মানুষকে আমরা সাথে রাখতে চাই। সমসাময়িক বিশ্বে মীজান খুব বেশী প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় আমরা তাঁর চুম্বক রচনাগুলো সময় সময় প্রকাশ করব এজন্য যে নতুন প্রজন্মের বাঙালি পাঠকের সাথে মীজান রহমানের কালজয়ী চিন্তাগুলোর মেলবন্ধন রচিত হয়। - সম্পাদক, আশ্রম
আমরা যারা দেশ ছেড়ে বিদেশে এসে বসবাস স্থাপন করেছি উন্নততর জীবনের সন্ধানে, তাদের পক্ষে হয়ত দেশের বর্তমান পরিস্থিতি, সেটা সমস্যাই হোক আর সম্ভাবনাই হোক, পুরোপুরি অনুধাবন করা সহজ নয়। আমরা দেশের অতীতকে যতটা বুঝি দেশের মানুষ হয়ত ঠিক ততটা বোঝে না, আবার দেশের লোক বর্তমানকে যত অন্তরঙ্গভাবে উপলদ্ধি করে আমরা তেমন করে বুঝি সেটা হয়ত জোর দিয়ে বলা যাবে না। আমরা যে চোখে দেশকে দেখি সেটাকে আমি বলি বাইরের চোখ। অতএব বাইরের চোখ যা দ্যাখে সেই একই জিনিস ভেতরের চোখ হয়ত দ্যাখে না। তবু একটা জিনিস অনস্বীকার্য---আমরা দেশ ছেড়েছি ঠিকই, কিন্তু দেশ আমাদের কখনোই ছেড়ে দেয় না, আঁকড়ে ধরে রাখে। দেশের প্রতি যে ভালোবাসা, যে অন্ধ, নির্বোধ আকর্ষণ, তার প্রাবল্য হয়ত দূরত্বের বহিঃসীমাতে আরো তীব্রতা অর্জন করে।
গত দুচারদশ বছরে বেশ ক’বারই দেশে যাবার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। ফিরে এসে প্রতিবারই প্রতিজ্ঞা করেছি, আর নয়, দেশে যাওয়ার পালা শেষ সারা জীবনের জন্যে। তারপর দুবছর যেতে না যেতেই মন আকুল হতে শুরু করে। দেশের মাটি প্রাণের গোপন প্রকোষ্ঠে আবার সজীব হয়ে ওঠে। অথচ যতবার গিয়েছি ততবারই দেখেছি দেশের মানুষ আর যেন টিকতে পারছে না, অতীষ্ঠ হয়ে উঠছে দৈনন্দিন জীবনের নানা বিড়ম্বনা আর স্বপ্নভঙ্গের হতাশাতে। আর যেন তারা থাকতে পারছে না ওখানে---আরাম আয়েসের অভাব সেজন্যে নয়, মানবজীবনের ন্যুনতম চাহিদাগুলোর দ্রুত অবনতির কারণে। আমরা যেমন আকুল হই দেশে যাবার জন্যে, কেউ কেউ হয়ত একেবারেই ফিরে যাবার স্বপ্ন পোষণ করেন, ওরা ঠিক একইভাবে আকুল হয়ে উঠছে দেশ থেকে বেরুবার জন্যে। এমন একটি দুঃসহ অবস্থা যে সৃষ্টি হয়ে যাবে স্বাধীনতার ৪১ বছরের মাঝে, বিশেষ করে পর পর চারটে গণতান্ত্রিক সরকারের হাতে শাসন পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হবার পর, সেটা আমরা, পুরনোদিনের মানুষ, যাদের মনে একাত্তরের স্মৃতি এখনো অনির্বান শিখার মত প্রদীপ্ত, যারা বুকভরা স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে এসেছি প্রবীনত্বের ধূসর প্রান্তরে, আমরা কখনোই কল্পনা করিনি। এ-অবস্থার জন্যে কে বা কারা দায়ী?
মানবচরিত্রের ধর্মই বোধ হয় এই যে, জাতীয় পর্যায়ে যে-কোন সমস্যাই ঘটুক সবকিছুর জন্যে একমাত্র সরকারকেই দায়ী করা হয়। যেন সাধারণ দেশবাসীদের নিজেদের কোনও ভূমিকাই নেই। আছে, সমান সমান না হলেও, বেশ মোটা পরিমান একটা ভূমিকা আছে। গণতন্ত্রকে সফল হতে হলে কেবল সরকারকে নয়, জনগণকেও পূর্ণ সজাগ ও সংলিপ্ত থাকতে হয় জাতির সার্বিক উন্নয়ন ও স্বপ্নসিদ্ধির প্রয়াসে। এই গণসংলিপ্ততার দিকটা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা সম্ভব ও প্রয়োজনীয়, তবে আমার আজকের আলোচানার প্রধান বিষয়বস্তু হবে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যেসব ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটেছে, অন্তত আমার দৃষ্টিতে, তার সংক্ষিপ্ত চিত্রায়ন।
জাতির সার্বিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও আশা-আকাঙ্খার বাস্তবায়নের জন্যে সবচেয়ে প্রয়োজন যে-জিনিসটার, সেটা হল একটি সুশীল সমাজ এবং সেই সমাজের কর্ণধার হিসেবে বলিষ্ঠভাবে দণ্ডায়মান একটি সত্যনিষ্ঠ, দক্ষ, আদর্শ সরকার। সেই সুন্দর সুশীল সমাজগঠনের পথে এই যে পর্বতপ্রমাণ বাধাবিপত্তির দেয়াল তৈরি হয়ে গেল আমাদের চোখের সামনে, সেই ক্রমপতনের প্রক্রিয়া ঠিক কোথায় এবং কখন শুরু হয়েছিল সেটা বস্তুনিষ্ঠভাবে নিরুপন করা হয়ত এ-প্রজন্মের পক্ষে একেবারেই সম্ভব নয়। অত্যন্ত বিতর্কমূলক প্রসংগ এটি।
অথচ সসস্যার উৎসমুখে পৌঁছাতে না পারলে সমস্যার শেষপ্রান্তে পৌঁছানো কোনদিন সম্ভব হবে কিনা সন্দেহ। আমার ব্যক্তিগত বিচারে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের সূচনাতে যে প্রতিশ্রুতিগুলোর পরিচয় দিয়েছিলেন তৎকালীন নেতানেত্রীরা, কালক্রমে সেই একই নেতৃবর্গ, যে-কোন কারণেই হোক, ওই আদর্শমালার কেন্দ্র থেকে বিচ্যুত হতে থাকলেন। ভবিষ্যত সংকটের পূর্বাভাস সেখানেই সুপ্ত ছিল বলে আমার বিশ্বাস। আজ এই যে অন্তহীন পাতালমুখি গতি আমাদের, তার প্রাথমিক যাত্রা শুরু হয়েছিল তখন থেকেই।
জাতিকে এগুতে হলে বলিষ্ঠ পদচালনা প্রয়োজন। পৃথিবীর কোন জাতিই এখন আর থেমে নেই, দ্রুতপদে এগিয়ে চলেছে নিজেদের লক্ষবস্তুর দিকে। তাদের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে হবে আমাদেরও। কিন্তু তার জন্যে সর্বাধিক দরকার হল একটি সুস্থ, সবল হৃদস্পন্দন, দুর্জেয় চিত্তশক্তি। সেই সবল স্পন্দনের মূল ভিত্তিটা কোথায়? আমার মতে তার সংবিধানে। একটা জাতির আশা-আকাংখা, তার মূল নীতি আদর্শ, তার বিশ্বাস অবিশ্বাস, সর্বোপরি, জাতিহিসেবে তার ভবিষ্যতের গন্তব্য কোথায় তার একটি সুস্পষ্ট নীলনক্সা এঁকে দেবার প্রচেষ্টা প্রকাশ পেতে হবে তাতে। সংবিধানই বলে দেবে আধুনিক জীবনের মানচিত্রে তার অবস্থান কোথায়, এবং কিধরণের সমাজ সে গঠন করতে চায়। সেদিক থেকে বিচার করলে বাংলাদেশের মূল সংবিধান ছিল তৎকালীন বিশ্বের অন্যতম সেরা দলিল----অগ্রমুখি, আধুনিক, ন্যায়নিষ্ঠ, গণসচেতন ও আশ্চর্যরকম বিশ্ব-মানবতাকেন্দ্রিক। চারটি প্রধান স্তম্ভ ছিল আমাদের সংবিধানেরঃ
জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ও ধর্মনিরপেক্ষতা।
এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময়কর ছিল শেষেরটি---ধর্মনিরপেক্ষতা, যার ব্যাপকতর তাৎপর্যটি উৎকৃষ্টভাবে প্রকাশ পায়, আমার মতে, ইংরেজির সেকুলারিটি শব্দটিতে। বিস্ময় বলছি এজন্যে যে বিপুল সংখ্যাধিক্যবিশিষ্ঠ কোন মুসলিম রাষ্ট্রই এর আগে বা পরে এরকম নিরপেক্ষ নীতি আদর্শ নিয়ে যাত্রা শুরু করেনি বা পারেনি। অন্যান্য দেশের তুলনায়, অন্তত এই একটি জায়গাতে, আমরা অনেকখানিই এগিয়ে ছিলাম। সেখানে দেশকে নিয়ে বুক ফুলিয়ে লোকের কাছে বলার মত সত্যি সত্যি কিছু ছিল আমাদের। মূলনীতিগুলোর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছিল এভাবেঃ
১। জাতির লক্ষ একটি সুস্থ সাবলীল গণতান্ত্রিক সমাজ গঠন করা;
২। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা যাতে সর্বপ্রকার শোষণ ও বৈষম্যমূলক আচরণ থেকে জনগণকে মুক্ত করা যায়;
৩। একটি সুসংহত সুশীল সমাজ তৈরি করা যেখানে আইনের শাসনই হবে সর্বেসর্বা। যার উর্ধে থাকবে না কোনও ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সরকার, যার লক্ষ হবে মানুষকে নিঃশর্তভাবে সকল অন্যায় অবিচার ও বাঁধবাধা ও শৃখংল থেকে মুক্ত করা;
৪। জাতির আর্থিক স্বাচ্ছল্য ও দারিদ্রমুক্তির পথ সুগম করা।
এতটা সম্মুখপন্থী সংবিধান একটি সদ্যজন্মলব্ধ দরিদ্র দেশের জন্যে সত্যি বড়ই সাহসী ও বিস্ময়কর পদক্ষেপ। ‘৭১এর রক্তস্নাত ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে রীতিমত বিপ্লবাত্মক। যুক্তরাষ্ট্রের জেমস ম্যাডিসন এবং তৎকালীন অন্যান্য গুণিজন দ্বারা নির্মিত ১৭৮৭ সালের সেই বিখ্যাত সংবিধান, পরবর্তীতে থমাস জেফার্সন দ্বারা পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত, যাকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ, এবং প্রায় অনুকরণীয় দলিল বলে আখ্যায়িত করা হয়, তার সঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়াবার ক্ষমতা আমাদের ছিল বটে। আমেরিকার সংবিধানে যেমন ছিল মুক্তবুদ্ধি, মুক্তচিন্তা, মুক্তভাবে লেখা বলা ও প্রচার করার স্বাধীনতা, ছিল আইনের শাসনের প্রতি গভীর সম্মান ও সাবধানী দৃষ্টি, আমাদের বাংলাদেশী সংবিধানে তার চেয়ে কম ছিল না কিছু। আমেরিকায় ছিল ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মানবাধিকারের ওপর বিশেষ জোর, আমাদের ঠিক একই জিনিস ছিল।
তখন দেশটির সরকারি নামকরণ হয়েছিলঃ বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্র। তার আগে পেছনে কোনও বিশেষণ যুক্ত করার প্রয়োজন বোধ করেননি সেসময়কার দূরদর্শী ও বিজ্ঞ সংবিধান প্রণেতাগণ। আমেরিকায় ধর্মচর্চার অবাধ স্বাধীনতা, এবং ধর্মগুরুদের প্রায় সাতখুন মাপের মত অধিকার ও সুযোগ সুবিধা, বাংলাদেশে ঠিক অতদূর যাওয়া হয়নি হয়ত, কিন্তু একটা কথা উল্লেখ করা হয়েছিল যা হয়ত পরবর্তীকালে খানিক সমস্যার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেটা হল এইঃ রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, যদিও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সমান স্বাধীনতা থাকবে তাদের নিজ নিজ ধর্ম চর্চা নির্ভয়ে চালিয়ে যাবার। আমার মত ধর্মবিরাগীদের চিন্তায় একটি স্বঘোষিত ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ জাতির জন্যে একটি বিশেষ রাষ্ট্রীয় ধর্ম থাকা কেমন যেন স্ববিরোধিতার মত মনে হয়েছে। হয়ত সেসময়কার পরিপ্রেক্ষিতে, বিশেষ করে চরম আর্থিক অবস্থায় মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর কাছে হাত পাতার প্রয়োজনেই, এটুকু আপস তাঁরা না করে পারেননি। কারণ যা’ই হোক ভবিষ্যতের অশনি সংকেত সম্ভবত সেই আপাত বিরোধিতার মধ্যেই সুপ্ত ছিল।
যাই হোক, নবগঠিত রাষ্ট্রের সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার তিনটি প্রধান শাখাতে বিভক্ত হয়ঃ
১। সংসদীয় শাখা (Legislative Branch)
২। নির্বাহী শাখা (Executive Branch)
৩। বিচার বা আইন শাখা (Judicial Branch)
বর্তমান বিশ্বের যে-কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র থেকে মৌলিক কোনও তফাৎ ছিল না আমাদের, এবং কার্যত না হলেও নীতিগতভাবে এখনও নেই। বড় কথা, যেহেতু সংবিধান অনুসারে আইন মূলত ‘অন্ধ’, অর্থাৎ আইনের চোখে ছোট বড়, রাজাবাদশা আর ইতরফকিরের কোনও তফাৎ নেই, ভেদাভেদ নেই অফিসের চাপরাশি আর বড় হুজুরে, সেহেতু আইনের শাখাটি ছিল সর্বাপেক্ষা স্বাধীন। তার অর্থ এই নয় যে আইনের লোকেদের ওপর আইন প্রযোজ্য হবে না, অবশ্যই হবে, ছোট হাকিম থেকে বড় হাকিম সকলেই সেই একই আইনের অধীনে নতশির। সেকারণেই হাকিম নিযুক্তির সময়ই এটা নিশ্চিত করে জেনে নিতে হয় যে লোকটি সকল ক্ষুদ্র স্বার্থের উর্ধে, এবং তাঁর প্রধান পরিচালক হল তাঁর উঁচুমানের জ্ঞানবুদ্ধি, বিবেক, নৈতিক চিন্তাচেতনা, এবং আইনপেশাতে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও আইনের ওপর অগাধ পাণ্ডিত্য। আমার বিশ্বাস এই গুরু দায়িত্ত্বটি তাঁরা বিশেষ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে গেছেন দেশের নানা দুর্যোগে দুঃসময়ে। বিবিধ সময়ে বিবিধ সরকারের বিবিধ বিরূপ আচরণের মুখেও।
উল্লেখ্য যে মূল সংবিধানটি ১১টি প্রধান খণ্ডে ভাগ করা হয়েছিল, আর তাতে ছিল সর্বমোট ১৫৩ টি দফা (Articles), উপরন্তু ছিল ৪ টি পরিশিষ্ট (Schedules)। অর্থাৎ মোটামুটি একটা সুন্দর বলিষ্ঠ দলিল, যা একটি স্বাধীন সার্বভৌম, আধুনিক রাষ্ট্রের উপযোগী শুধু নয়, অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করার মত। বাংলাদেশের প্রথম ও মূল সংবিধানটি আমুষ্ঠানিকভাবে আইনসভার অনুমোদন লাভ করে ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর। কিন্তু তার অনতিকাল পরেই ‘ঈশান গগনে গরজি উঠিল মেঘ’। একে একে শুরু হয়ে গেল সংশোধনের পর সংশোধন (Amendment)। যাকে ‘সংশোধন’ না বলে, আমার মতে, বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের মত দুর্বল ও অনুন্নত রাষ্ট্রের বেলায়, ‘দূষণ’ বলে আখ্যায়িত করা উচিত। ২০১১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রের সংবিধান ১৪ বার ‘সংশোধিত’ হয়েছে। এবং প্রতিবারই লক্ষ ছিল, সংবিধানকে নিজেদের ইচ্ছামত বাঁকিয়ে জুকিয়ে তাদের দলীয় মর্জিমাফিক দেশ চালনা করা, আইনের ‘অনুমোদন’ সহকারে।
অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে প্রথম সংশোধনটি সংঘটিত হয় প্রথম জাতীয় সরকারের শাসনকালেই---১৯৭৩ সালের ১৫ই জুলাই। তাতে আইন করে পাস করে নেওয়া হয় এই বিধিটি যেঃ ‘কোনও ব্যক্তি গণহত্যা, মানবতাবিরোধী অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধ বা অনুরূপ কোন অপরাধে অভিযুক্ত হলে তাকে সংবিধানপ্রদত্ত কতগুলো মৌলিক অধিকার’ থেকে বঞ্চিত করা হবে। আপাতদৃষ্টিতে, এবং দেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসের আলোকে, এটা হয়ত তেমন্ আপত্তিকরও ছিল না। কিন্তু তার পরবর্তী যে ‘সংশোধন’টি প্রবর্তন করা হয় তাতে বলা হয় যে ‘জরুরি অবস্থায় নাগরিকদের কাছ থেকে কতগুলো স্বাধীনতার অধিকার স্থগিত রাখা হবে’। আপাতদৃষ্টিতে এটাও হয়ত যুক্তিসঙ্গত মনে হবে, এমনকি উচ্চশিক্ষিত, বুদ্ধিজীবিদের চোখেও। কিন্তু আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে একটা আধুনিক, উন্নত ও সভ্য জাতির নাগরিকদের ন্যুনতম অধিকারগুলোর প্রধান প্রহরী কে? সরকার তো বটেই, তবে মূলত সেটা সংবিধান। ওটার শেকড় নিয়ে যখনই টানাটানি শুরু হয়ে যাবে তখনই সূচিত হবে জাতির চিত্তশক্তির ক্রমিক্ অবক্ষয় ও রক্তক্ষরণ। পাশ্চাত্য আইনের সবচেয়ে গোড়ার দর্শন কি? Presumption of Innocence. এটা ওদের সভ্যতার ভিত্তিপ্রস্তর। আমরা সেটা মানি বা না মানি, জ্ঞাতে অজ্ঞাতে আমরা বহিরাগত অভিবাসীরা এই নীতিটিরই সর্বপ্রকার সুফল ভোগ করে যাচ্ছি। এদেশে ‘সব অপরাধই প্রমাণসাপেক্ষ, এবং সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কোন আসামীকে দোষী আখ্যায়িত করার অধিকার নেই কারুর’। দুঃখের বিষয় যে আমাদের সংবিধানে তাত্ত্বিকভাবে এটা বর্ণিত ছিল ঠিকই, কিন্তু কখনোই সেটা জাতির মজ্জাতে প্রবেশ করার সুযোগ পায়নি। একটা সুযোগ ছিল প্রথম গণতান্ত্রিক সরকারের। কিন্তু তাঁদের ১৯৭৩ সালের সংশোধন দ্বারা সে-সুযোগটি তাঁরা হেলায় হারিয়ে ফেললেন। অন্তত আমার মতে।
সত্যিকার মারাত্মক ‘সংশোধনী’ কিন্তু সেটা ছিল না। মারাত্মকটি এল পরে। ১৯৭৪ সালের ২৮শে নভেম্বরে গৃহিত চতুর্থ amendment এ, যাতে ছিল নিম্নলিখিত নীতিমালাঃ
১। পার্লামেন্টারী প্রথার পরিবর্তে প্রেসিডেন্সিয়েল শাসন শুরু হবে;
২। বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থলে একদলীয় পদ্ধতির সূচনা হবে;
৩। জাতীয় সংসদের ক্ষমতা হ্রাসপ্রাপ্ত করা হবে;
৪। জাতীয় সংসদের মেয়াদ বাড়ানো হবে;
৫। বিচার বিভাগের ক্ষমতা কমানো হবে;
৬। মৌলিক অধিকারাদি প্রতিরক্ষা ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের একচ্ছত্র এক্তিয়ার বাতিল করা হবে।
পাঠক এবং শ্রোতাদর্শকদের স্মরণ থাকার কথা যে এই সংশোধনী আইন পাস হবার মাত্র ৮ মাসের মধ্যে দেশের ভাগ্যাকাশে চরম দুর্যোগ নেমে এসেছিল, ১৫ই আগস্ট। কেবল তা’ই নয়, সেই অবিশ্বাস্যরকম বর্বর হত্যাকাণ্ডের তিন মাস পর আরো এক অবিশ্বাস্য নাটকের অবতারণা হয় ৩রা নভেম্বরের প্রত্যুষলগ্নে----ঢাকার জেলখানার তথাকথিত সংরক্ষিত এলাকায়।
যে স্বাধীনতা অর্জন করতে প্রাণ দিয়েছিলেন ’৫২ এর চার বঙ্গসন্তান, ‘৭১এর সশস্ত্র সংগ্রামে নৃশংসভাবে নিহত হয়েছিলেন বহু লক্ষ নিরপরাধ বাঙালি, সম্ভ্রম হারিয়েছিলেন শতসহস্র অসহায় নারী, সে স্বাধীনতার নির্মাতাদের, সেই স্বপ্নপুরির প্রদীপ্ত সারথিদের, গুটিকয় অভিশপ্ত গুলির আঘাতে চিরতরে ছিনিয়ে নেওয়া হয় জাতির বুক খণ্ডে খণ্ডে বিদ্ধ করে। গুটিকয় তুচ্ছ গুলি কেড়ে নেয় জাতির অতীত গৌরবকে, সাথে সাথে ভবিষ্যতের স্বপ্নপুরির সকল সম্ভাবনাকেও। দেশকে যারা স্বপ্নের তুলি দিয়ে গড়ে তুলতে পারতেন, পারতেন জাতির শতবছরের নিপীড়িত, নিস্পেষিত জনগণকে দারিদ্র্যমুক্ত স্বাধীনতার উন্নত সিংহদ্বারে পৌঁছে দিতে, সেই আশার মশালধারী পথিকৃৎদের আমরা হারালাম কতগুলো মূর্খ, অর্বাচীন সৈনিকের অন্ধ জৈবিক বশ্যতার কারণে। জাতির সেই ক্ষতবিক্ষত দেহ কখনোই আর সেরে উঠবার সুযোগ পায়নি। কোনদিনই সেই ভয়াবহ দুঃস্বপ্নগুলো শুভসুন্দর সুখস্বপ্ন হয়ে প্রস্ফূটিত হয়ে উঠতে পারেনি।
কিন্তু তার পর? তারপর কি হল জাতির জীবনে? যে একদলীয় প্রস্তাব গৃহিত হয়েছিল সংসদীয় প্রক্রিয়াতে, ‘৭৫এর জানুয়ারিতে, সেটা আর ‘একদলীয়’ থাকার সুযোগ পেল না, হয়ে গেল ‘একনায়কীয়’ সামরিক স্বৈরতন্ত্র। একনায়ক সামরিক শাসন কখনও কোনদেশেই কোন স্থায়ী কল্যান সাধন করতে সক্ষম হয়নি----ইতিহাসে বারবার তা পরীক্ষা হয়েছে, বারবারই সেটা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।
মরার গায়ে খাঁড়ার ঘায়ের মত ৭৫-৭৭ সালের সামরিক শাসনকালের কোনও এক অশুভ মুহূর্তে রাষ্ট্রপতির বিশেষ ঘোষণা অনুযায়ী সংবিধানের মূল হৃদপিণ্ডটি---ধর্মনিরপেক্ষতা---সেটি উপড়ে ফেলা হয় এক বয়ানেঃ ইসলামই জাতির একমাত্র পবিত্র ধর্ম, যেখানে সর্বশক্তিমান আল্লার ওপর নিরংকুশ আস্থা ও বিশ্বাসসম্পন্ন জাতি পূর্ণ ও ঐকান্তিকভাবে নির্ভরশীল। রাষ্ট্রীয় কুড়ালের এক কোপেই ‘নিরপেক্ষতা’র শেকড় চিরতরে উৎপাটিত। দেশের ধর্মভীরু মানুষ একবার আল্লারসূলের রাজত্বে বাস করার স্বাদ পেলে আর কখনোই ভিন্ন জগতের শাসন মানতে চাইবে না। সুতরাং এই দেশ কখনো যেমন পুরোপুরি ধর্মনিরপেক্ষ ছিল না, ‘৭৫এর সেই কুড়ালের ঘা’টির পর কোনদিন হবেও না। অন্তত আমার মতে। আজকের বাংলাদেশে এই যে ধর্মীয় গোঁড়ামির অব্যাহত অরাজকতা, এই যে পীর-দরবেশ, আল্লাহাফেজ আর আব্রু-আবরণের মহামারি, তার সূত্রপাত, আমার ব্যক্তিগত বিচারে, ’৭৫ থেকে ’৯০ পর্যন্ত সেই যে একটানা সামরিক শাসন, তাতেই।
মজার ব্যাপার যে সামরিক শাসন কোনও আধুনিক, উন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের জনগণের জন্যে কাম্য বা হিতকর না হলেও আমাদের দেশটিতে এর প্রতি একটা অদ্ভুত, দুর্বোধ্য, আকর্ষণ লক্ষ করেছি আমি। সেই পাকিস্তান আমল থেকেই। আইয়ুব খান যখন বন্দুকের জোরে গোটা দেশের শাসনক্ষমতা নিজের করায়ত্ত করে নিলেন গণতান্ত্রিক অরাজকতা ও জনগণের দুঃখদুর্দশার দোহাই দিয়ে, তখন ঢাকার রাজপথে আমি সাধারণ মানুষকে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠতে দেখেছি। পুরো একটা বছর পূর্ব পাকিস্তানের সবচেয়ে জনপ্রিয় মানুষ ছিলেন আইয়ুবনিযুক্ত জেনারেল আজম খান। তাঁর জনপ্রিয়তা এতটাই তুঙ্গে উঠে যায় যে নিজের গদির ভয়ে লোকটাকে গভর্নরের পদ থেকে অব্যাহতি দিয়ে পশ্চিমের সমরশিবিরে ফিরিয়ে নিলেন আইয়ুব সাহেব।
তারপর বড়রকমের সামরিক উত্থান ঘটে দেশ স্বাধীন হবার পর, ‘৭৫এ। তখনও ঠিক একই প্রতিক্রিয়া লক্ষ করেছেন ঢাকার অভিজ্ঞ পর্যবেক্ষকরা। আমি তখন দেশের বাইরে, তাই স্বচক্ষে দেখবার সুযোগ হয়নি। কিন্তু শুনেছি মিষ্টির দোকান সব খালি হয়ে গেছে। ঠিক যেমনটি হয়েছিল ১৯৫৮ সালে। আমাদের দেশে এই যে এত ডায়েবেটিজের ছড়াছড়ি তার কারণ আছে। এমনিতেই মিষ্টির প্রতি বাঙ্গালির একটি সহজাত দুর্বলতা, তার ওপর একেকটি সামরিক ক্যুতে এক আধমণ চিনি প্রবেশ করে আমাদের রক্তস্রোতে। বহুমূত্র হবে না তো কি হবে!
হাসির কথা, আবার হাসির কথাও নয়। কষ্টের কথা। লজ্জার কথা। আসলে ‘গণতন্ত্র’ শব্দটা আমরা ভাল বুঝি না। সাধারণ অল্প বা অর্ধশিক্ষিত জনগণ তো না’ই, বড় বড় ডিগ্রিওয়ালা হোমরা চোমরারাও কতখানি বোঝেন ভাববার বিষয়। রাস্তার লোকেদের কাছে গণতন্ত্র মানে নির্বাচন, ভোট, কলাগাছ আর শাপলার বাক্স, টিকসই, একটুকরা কাগজ বাক্সতে ফেলে দেওয়া ব্যস, তারপরই জীবনের সব দুঃখকষ্ট দূর হয়ে যাবে। গণতন্ত্র মানে আওয়ামী লীগ বা বিএনপি, কিংবা জাতীয় পার্টি, এর বাইরে কারো কোন দায়িত্ব নেই। সব দায়িত্ব নির্বাচিত সরকারের। সে কারণেই থমাস কার্লাইল নামক এক বিখ্যাত লেখক লিখেছিলেন এক জায়গায়ঃ
“In the long run every government is the exact symbol of its people, with their wisdom and unwisdom”. এটা বিংশ শতাব্দীর কথা। তার বহু আগে, ১৮১১ খৃষ্টাব্দে জোসেফ মারি দ্য ম্যাতর নামক এক ভাষ্যকার লিখেছিলেনঃ
“Every country has the government it deserves”. শুনতে কর্কশ লাগে, তবে অপ্রিয় সত্য কি বরাবরই তা নয়? গ্রীক দার্শনিক প্ল্যাটো (খৃঃপূঃ৪২৭-৩৪৭), প্রায় একই সুরে বলে গেছেন আড়াই হাজার বছর আগেঃ “ Like man, like state; …governments are made of the human natures which are in them”. অবশ্য একটা কথা মানতেই হবে আমাদের যে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের বয়স মাত্র ২২ বছর। এত অল্প সময়ে কোন জাতিই, শিক্ষাদীক্ষায় আর জ্ঞানবিজ্ঞানে যতই অগ্রসর হোক সেজাতি, গণতন্ত্রের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে পারেনি। জিনিসটা প্রকৃতিগতভাবেই অত্যন্ত ঢিলেগতি। ইউরোপ-আমেরিকা একদিনে গণতান্ত্রিক হয়ে ওঠেনি, প্রায় পুরো একটা শতাব্দী লেগে গিয়েছিল গণতন্ত্রের কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছাতে। গণতন্ত্রের একমাত্র উপাদান নির্বাচন বা গণভোট নয়, এমনকি প্রধান উপাদানও নয়। প্রধান উপাদান মানসিক ও চারিত্রিক। গণতন্ত্র মানে জনগণের সার্বিক সহযোগিতা ও সমন্বয়---নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেই একটি একক জাতিসত্তা তৈরিতে সমানভাবে হাত বাড়িয়ে দেওয়া, এই মানসিকতা প্রস্তুতের জন্যে যে-কটি উপকরণ আবশ্যিকভাবে দরকার তার মধ্যে অন্যতম হল ধর্মনিরপেক্ষতা (কারণ তা নাহলে ধর্মভিত্তিক বৈষম্যমূলক আচরণ একেবারেই অনিবার্য হয়ে দাঁড়াবে)। দুই, নারী-পুরুষের সমান অধিকার (তা নাহলে নারীর প্রতি আমাদের গতানুগতিক তাচ্ছিল্যমূলক আচরণ কখনোই বন্ধ হবে না, তাদের প্রতি সত্যিকার সম্মানবোধ সৃষ্টি হবে না বাংগালি পুরুষের মনে)। তিন, আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা যাতে ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষাতে ছাত্রছাত্রীদের সমান পারদর্শীতা থাকবে, যাতে আধুনিক বিজ্ঞানের অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারের কথা যেমন জানবে তারা তেমনি করে তারা গড়গড় করে আবৃত্তি করে যেতে পারবে একাধারে রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-জীবনানন্দ-শামসুর রাহমান থেকে সেক্সপিয়ার-অডেন-হুইটম্যান-বোদলেয়ার। অর্থাৎ একটা পূর্ণাঙ্গিন শিক্ষায় শিক্ষিত প্রজন্ম----যা আজকের বাংলাদেশে হচ্ছে না। মজার ব্যাপার হল যে আজকের স্বাধীন বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা হয় বাংলা শিখছে মোটামুটি ভাল, কিন্তু ইংরেজিতে লবডঙ্কা। নতুবা ইংরেজি শিখছে সাহেবদের মত, এবং বাংলা বলছে সেই সাহেবদেরই মত। এর ফলে কি দাঁড়াচ্ছে সমাজের চেহারা? একটা অত্যন্ত বিসদৃশ, বিকৃত জীব, যারা দুপায়ে হাঁটতে শেখেনি, হয় বাঁপায়ে, নয় ডানপায়ে ভর দিয়ে হাঁটে। এর নাম ব্যালেন্সেড সোসাইটি নয়। ভাবতে হাসি পায়, সাথে সাথে কান্নাও পায় যে দেশ যখন স্বাধীন ছিল না, মানে পাকিস্তানেরও আগেকার কথা, যে তখন এই ‘ব্যালেন্স’ জিনিসটা ছিল, যেকারণে আমরা পুরনো যুগের মানুষরা ইংরেজি-বাংলা দুটোই মোটামুটি সামলাতে পারি প্রায় সমান দক্ষতা বা অদক্ষতার সাথে।
উপরোক্ত শর্তগুলোর কোনটাই সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দেশে সেটা বোধ হয় চরম আশাবাদীরাও দাবি করতে পারবে্ন না। আসলে আমাদের দেশটির প্রধান প্রতিবন্ধকটাই সেখানে----একচল্লিশ বছরে কোনও প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে পারিনি আমরা। যা’ই নির্মাণ করি সবই ব্যক্তি মালিকানা বা কোন-না-কোনভাবে ব্যক্তিনির্ভর। সুতরাং সে ব্যক্তিটি যখন্ ইহধাম ছেড়ে চলে যান তখন তাঁর ইমারতটিরও আর বাপ-মা থাকল না। এই ব্যক্তিকালচার আমাদের দেশটিকে কুঁড়ে কুঁড়ে ক্ষয় করে ফেলল। আমরা হয় পূজা করি একটা বড় নেতাকে, নয়ত পায়ের নিচে পিষে মেরে ফেলি। কখনও শিখিনি কিভাবে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিজের পায়ের ওপর ভর করে চলতে হয়---কিভাবে ব্যক্তিকে অতিক্রম করে একটা স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়তে হয়। পারিনি বলেই আমরা মনে করি যাকে ভোট দেব সে’ই আমাদের সব সমস্যা সমাধান করে দেবে। না, তা দেয় না, কেউ তা দিতে পারেনা। সমস্যা সমাধানের জন্যে আপনাকেও কাজে যেতে হবে, সৎভাবে নিজের দায়িত্বটুকু পালন করতে, নিয়মিত ট্যাক্স দিয়ে যেতে হবে, আইনের শরণাপন্ন হতে হবে যখনই কোন অনিয়ম ব্যত্য্য পরিলক্ষিত হয় কোথাও। এর সবকিছুই একটি গণতান্ত্রিক দেশের সাফল্যের জন্যে অবশ্যপ্রয়োজনীয়।
দুর্ভাগ্যের বিষয় এর প্রায় কোনটাই নেই আমাদের সমাজে। সেই কালচারটাই তৈরি করে নিতে পারিনি আমরা।
পরপর চারটে বেসামরিক গণতান্ত্রিক সরকারের শাসনকালে দেশের জনজীবনের সত্যিকার কোনও উন্নতি হয়েছে কিনা সেটা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়, আমি দেশে থাকিনা। কালেভদ্রে যাই বেড়াতে। নিমন্ত্রন খেয়ে বসুন্ধরা শপিং মলে যাই কেনাকাটা করে খইমুড়ির ঠোঙ্গা নিয়ে পশ্চিমের ছেলেছোকরাদের মত চিবোতে চিবোতে হালের ছবি দেখতে ঢাকার নতুন নতুন মুভিহলে। তারপর ক্যানাডা-আমেরিকার অভ্যস্ত আরাম-আয়েসের জীবনে প্রত্যাবর্তন করে প্রথমে যাই ক্লিনিকে চেক-আপটা করিয়ে নিতে (বলা তো যায় না ধূলাময়লায় মাস দুমাস বাস করার পর কখন কোন ভাইরাস ঢুকে গেছে শরীরে), এবং অবশেষে নিশ্চিন্ত হয়ে দেশের খবর দিই উৎসুক শ্রোতাদের---দেশের যা উন্নতি হয়েছেরে ভাই, বলিসনে। ইয়াব্বড় সব দালান, আমেরিকান কায়দায় বানানো বিরাট সব শপিং মল, দামি দামি রেস্টুরেন্ট, ইন্টারন্যাশনাল মানের হোটেল, ১২টা টিভি চ্যানেল, লোকের হাতে হাতে সেলফোন, চাকরানিদের হাতে হ্যাণ্ডব্যাগ, ঘড়ি, সোনার চুরি, বাহ, ভাগ্যিস, দেশটা স্বাধীন হয়েছিল। বন্ধুরা খবর শুনে মুগ্ধ। কিন্তু পর্দার পেছনে যে আরেকটা ছবি আছে সেটা আপনি যেমন জানেন আমিও জানি। উন্নতি যে কিছুটা হয়নি তা নয়, অনেকই হয়েছে। কিন্তু যা হতে পারত, যা হবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে দেশটার জন্ম হয়েছিল তার একাংশও হয়নি। বড় কথা আমরা মূল আদর্শ থেকে বিপুলভাবে স্খলিত হয়ে পড়েছি।
প্রশ্ন উঠেছেঃ সুশীল সমাজ গঠিত হতে পারছে না। ‘মুক্তিযুদ্ধের চেতনা’বহ নাগরিক তৈরি হতে পারছে না। (‘মুক্তিযুদ্ধের চেতনা’ বলতে ঠিক কি বোঝায় সেটা আমার মাথায় এখনও পরিষ্কার হয়নি) তারপর প্রশ্ন উঠেছেঃ সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারছে না। যানজট, ধর্মঘট, জনজট, বিদ্যুৎ, পানি, খাদ্য, দ্রব্যমূল্য, বায়ুদূষণ, পরিবেশদূষণ, ভেজাল, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, সন্ত্রাস, ছাত্রদৌরাত্ম্য, সীমাহীন চুরিচামারি খুনখারাবি ধর্ষণ, গণধর্ষণ, পুলিশের অত্যাচার----সে এক অন্তহীন তালিকা।
সবই সরকারের দায়িত্ব! অন্তত সাধারণ মানুষের চোখে, অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তিদের চোখেও। কিন্তু, এখানে সত্যি সত্যি সরকারের করনীয়টি কি। কি হওয়া উচিত যাতে করে একটা দক্ষ সরকারের সংগামাফিক কর্তব্য সমাপন করা যায়? ইংরেজিতেঃ what does it mean by a good government? এখানেও আমি প্রথমেই প্ল্যাটো থেকে শুরু করার লোভ সামলাতে পারছিনা। তাঁর একটা অমূল্য বাণী ছিলঃ “Until philosophers are kings, or the kings and princes have the spirit and power of philosophy, and wisdom and political leadership meet in the same man….cities will never cease from ill, nor the human race”.
(যতক্ষণ না দার্শনিক হচ্ছেন নৃপতি, অথবা রাজাবাদশাদের মনোভাবে প্রকাশ পাচ্ছে দার্শনিকের অন্তর্শক্তি, প্রকাশ পাচ্ছে তার প্রজ্ঞা ও রাজনৈতিক নেতৃত্বদানের গুণাবলী ততক্ষণ নগরবাসীদের লাঞ্ছনার জীবন শেষ হবে না, শেষ হবে না গোটা মানবকূলের দুঃখদুর্দশা।)
মানছি যে প্ল্যাটোর সময় থেকে আমাদের সময় এবং সমাজ-সভ্যতা আগাগোড়া ভিন্ন। তাছাড়া উনি ছিলেন স্বাপ্নিক, বিশুদ্ধতাবাদী সাধুপুরুষ, সবকিছুই তাঁর মহৎ আদর্শমাফিক হওয়া চাই, যা তাঁর সময়কালেও অবাস্তব বলে গণ্য করা হত। তাঁর রাজনৈতিক মতবাদকে সেকারণেই হয়ত ‘ইউটোপিয়ান’ বলে আখ্যায়িত করা হয়। তা সত্ত্বেও আমি তাঁর বাণী নিয়ে এলাম আমার এ-বক্তব্যে কেবল তার অন্তর্নিহিত নির্যাসটুকু তুলে ধরার জন্যেঃ নেতাকে রাজার যোগ্য ব্যক্তিত্ব থাকতে হবে, আর থাকতে হবে দার্শনিকসুলভ বিষয়বৈরাগ্য ও জ্ঞানাদর্শ। আমার ব্যক্তিগত মতে। এ গুণগুলো আজকের গণতান্ত্রিক যুগেও সমান কাম্য। এগুলো অত্যন্ত দুর্লভ, জানি, কিন্তু এগুলো যেখানে আছে সেখানে জাতির অগ্রগতি অপ্রতিহত গতিতে চলবে সেটা আশা করা যায়।
সুশাসন বা সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থার ধারণার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন আমেরিকার অন্যতম শীর্ষস্থানীয় প্রেসিডেন্ট থমাস জেফার্সন। তাঁর বক্তব্য ছিল এইঃ “The care of human life and happiness and not their destruction is the only legitimate object of good government.”
তবে নীতিগতভাবে কথাটার একটা সংগা থাকা দরকারঃ সুশাসন কাকে বলে? তার কি কি উপাদান? রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে উপাদানগুলো হচ্ছে এরকমঃ ১।রাষ্ট্রের সকল অংগপ্রত্যঙ্গের সমান সংযোগ ও সংশ্লিষ্ট্রতা; ২।শাসনপ্রণালীর সুস্পষ্ট স্বচ্ছতা; ৩।সুশাসনের আরেক অর্থ আইনের শাসন, অর্থাৎ রাষ্ট্রের সকল ব্যক্তি গোষ্ঠী দল গোত্রের উর্ধে হল আইন, যা অমান্য হলে জাতির সমস্ত দেহটাই আহত হয়ে যায়, এবং নিয়মিতভাবে অমান্য হতে থাকলে সে-জাতি কখনোই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না; (গ্রেট ব্রিটেনে সেজন্যেই ম্যাগনাকার্টা নামক যুগান্তকারি সনদ তৈরি করা হয়েছিল ১২১৫ খৃষ্টাব্দে, এবং অনেকটা তারই ফলশ্রুতিতে সেদেশে কখনোই বড়রকমের গৃহযুদ্ধজাতীয় কোনও অপ্রীতিকর সংঘাত ঘটেনি); ৪।জবাবদিহিতা, যেটা একটি গণতান্ত্রিক সরকারের জন্যে একেবারেই আবশ্যিক। তারা কিভাবে সরকারের দৈনন্দিন কায়কারবার পরিচালনা করছেন, সরকারি তহবিল কে কিভাবে ব্যবহার করছেন তার জবাবদিহি তাদের করতেই হবে জনগণের কাছে, নইলে তারা নিজেদের বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলতে পারেন; ৫।জনমত প্রতিষ্ঠা, যার জন্যে সংবাদ মাধ্যমের আন্তরিক সহযোগিতা ঐকান্তিকভাবে বাঞ্ছনীয়; ৬।সরকার এবং তার শাখাপ্রশাখাগুলোর সর্বদা গণমুখি হয়ে থাকা এবং মাটিতে কাণ পেতে থাকা; ৭।সমতা ও সর্বজনসহযোগিতা সৃষ্টির পথ সুগম করা; ৮।সবশেষে আছে সরকারের সকল নীতিমালার কার্যকরিতা ও প্রয়োগযোগ্যতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া।
এই উপাদানগুলো কি আমাদের গণতান্ত্রিক সরকারগুলোর একটিও মেটাতে সক্ষম হয়েছেন? আপনারাই বিচার করুণ। ভবিষ্যতে কি কখনও পারবেন তারা? সেটা নির্ভর করে শুধু নির্বাচিত সরকারের ওপর নয় আপনার আমার মত সকল নাগরিকের ওপর। সমস্যা অনন্ত, তেমনি আমি বিশ্বাস করি সম্ভাবনাও একই রকম অনন্ত।প্রথমত গণতান্ত্রিক সরকারকে ফিরে যেতে হবে মূল সংবিধানে। দ্বিতীয়ত আপনি আমি সকল দেশপ্রেমিক নাগরিককে কাস্তে কোদাল নিয়ে মাঠে নামতে হবে সরকারের সহায়তা দেবার জন্যে। আমি সবসময়ই একটা উক্তি শোনাই চেনাজানা স্বদেশীদেরঃ দেশের সমস্যা সমাধান করার দুটি পথ। একটি সোজা পথ, আরেকটি কঠিন পথ। সোজা পথটি হলঃ নিজেকে সোজা করা। কঠিনটি হলঃ নিজেকে বাদ দিয়ে পৃথিবীর আর সবাইকে সোজা করা। নাকি বলব, দ্বিতীয়টিই বেশি শক্ত?
১৭ই জুন ‘১২
মুক্তিসন ৪১


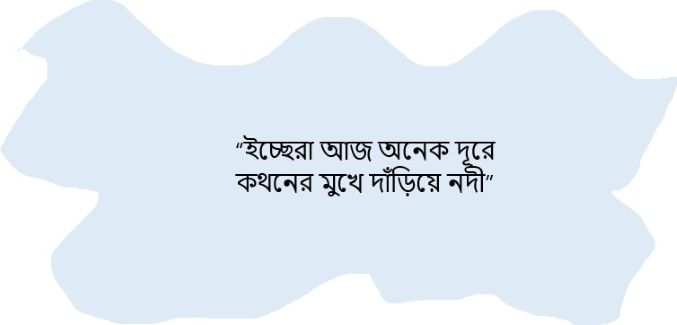
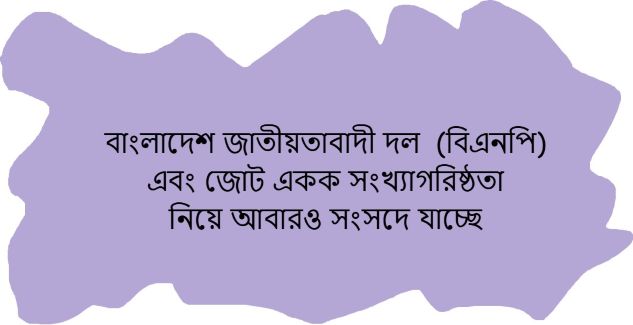
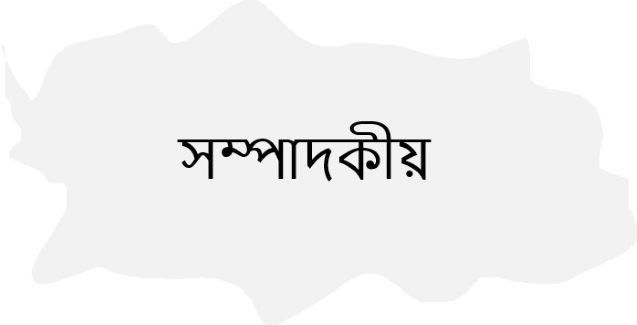
এখনও কোনো মন্তব্য নেই। প্রথম মন্তব্যটি করুন!